লাইটিক চক্র ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য | Difference between lytic cycle and lysogenic cycle
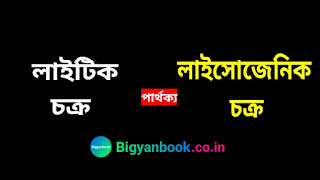
নমস্কার স্বাগত আপনাকে বিজ্ঞানবুক এ। এই আর্টিকেলে আমরা জানবো লাইসোজেনিক চক্র এবং লাইটিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। • লাইটিক চক্র কী? | What is Lytic cycle? যে পদ্ধতিতে ফাজ ভাইরাস পোষক ব্যাকটেরিয়া কোশে প্রবেশ করে জনন সম্পন্ন করে এবং অপত্য ভাইরাসগুলি পোষক দেহের বিদারণ বা লাইসিস ঘটিয়ে নির্গত হয় তাকে লাইটিক চক্র বলে। • লাইসোজেনিক চক্র কী? | What is Lysogenic cycle? যে পদ্ধতিতে ফাজ ভাইরাস পোষক ব্যাকটেরিয়ার কোশে প্রবেশ করার পর ভাইরাল DNA, ব্যাকটেরিয়াল DNA -এর সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং ব্যাকটেরিয়াল DNA-এর সঙ্গে একত্রে প্রতিলিপি গঠন করে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে পোষক ব্যাকটেরিয়ার কোশের বিদারণ ঘটিয়ে মুক্ত হয় না তাকে লাইসোজেনিক চক্র বলে। লাইটিক চক্র ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য | Difference between lytic cycle and lysogenic cycle ১) লাইটিক চক্র : লাইটিক চক্রের মাধ্যমে সমগ্র ভাইরাসটি গঠিত হয়। ১) লাইসোজেনিক চক্র : লাইসোজেনিক চক্রের মাধ্যমে কেবলমাত্র ভাইরাল DNA অনুর প্রতিলিপি গঠিত হয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভাইরাসের সৃষ্টি হয় না। ২) লাইটিক চক্র : লাইটিক চক্রে পোষ...




